অজানার ভয়
অজানা জিনিসের ভয় মানুষের প্রাচীন ও সাধারণ এক অনুভূতি। এই ভয় তখনই আমাদের মনে
আসে যখন সামনে কী হতে যাচ্ছে তা আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না। তখন মনে হয়,
সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।
একটা ছোট্ট শিশু যেমন অন্ধকারে ভয় পায়, তেমনি কোনো সমাজও বড় ধরনের পরিবর্তনের
মুখে ভীত হয়ে পড়ে। এই ভয় মানুষের ভাবনা, আচরণ আর সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব
ফেলে।তবে কেউ যদি সাহস করে এই ভয়কে মোকাবিলা করে, তাহলে সেটা তার নিজের উন্নতি,
মানসিক শক্তি এবং জীবনকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ তৈরি করে।
সূচিপত্রঃ অজানার ভয়
যে কারনে আমরা অজানাকে ভয় পাই
অজানার ভয় মানব জাতির বিবর্তনের ইতিহাসের সাথে গভীরভাবে জড়িত আছে। প্রাগৈতিহাসিক
যুগে অপরিচিত পরিবেশ, অজানা প্রাণী বা অপরীক্ষিত খাবার প্রায়ই মানুষদের প্রাণঘাতী
বিপদের মুখে ঠেলে দিত। বেঁচে থাকার জন্যে আদিম মানুষদের এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়
এড়িয়ে চলতে হতো।
আদিম মানুষদের মধ্যে যারা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ভয় পেত এবং তা নিয়ে সতর্ক থাকত,
তাদের টিকে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি করার সম্ভাবনা বেশি ছিল। ফলে তারা তাদের এই সতর্ক
আচরণ এবং মানসিকতা পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে পারত। সময়ের সাথে সাথে এই ধরনের
আচরন মানব প্রকৃতির অংশ হয়ে যায়।
এই ভয়ের অনুভূতি মানুষের মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা নামের একটি বিশেষ অংশের সঙ্গে
জড়িত। অ্যামিগডালা আমাদের মস্তিষ্কে বিপদ চিনে ফেলে এবং ভয়ের প্রতিক্রিয়া তৈরি
করে,বিশেষ করে যখন কোন কিছু নতুন বা অনিশ্চিত লাগে। প্রাচীনকালে আমাদের
পূর্বপুরুষদের জন্য এটি খুব দরকারি ছিল; কারণ তারা বিপদ বুঝে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত
নিতে পারত, আর সেটাই অনেক সময় জীবন বাঁচানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত।
তবে বর্তমান যুগে আমরা যে ধরনের বিপদ নিয়ে ভয় পেয়ে থাকি সেগুলো সাধারণত প্রাণঘাতী
হয় না। আধুনিক জীবন তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হলেও, আমাদের মস্তিস্ক এখনও অনিশ্চয়তার
প্রতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া দেখায়। কারণ আমাদের মস্তিস্ক এখনো
সম্পূর্ণভাবে আধুনিক জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি।
ফলে নতুন চাকুরি শুরু করা, নতুন শহরে যাওয়া, বা অপরিচিত লোকেদের সাথে কথা বলার
সময়ে মানুষ এখনো একধরনের অস্বস্তিবোধ অনুভব করে থাকে। বাস্তব বিপদের কোন সম্ভাবনা
না থাকলেও এই ভয়গুলো আমাদের কাছে একবারে সত্যিকারের বলেই মনে হয়ে থাকে। এটি
প্রমান করে যে আমাদের প্রাচীন বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি বা Survival Instinct এখনো
আমাদের আধুনিক আচরনে প্রভাব ফেলে চলেছে।
অজানার ভয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো
মানসিকভাবে অজানার ভয় বিভিন্ন উদ্বেগজনিত সমস্যার সাথে গভীরভাবে জড়িত। দীর্ঘদিনের
দুশ্চিন্তা (Generalized Anxiety Disorder) এবং ফোবিয়ার মতো মানসিক সমস্যা অনেক
সময়ই অনিশ্চয়তা সামলাতে না পারার কারনে হয়ে থাকে। আমাদের মস্তিস্ক আগেভাগে কী হতে
পারে তা বুঝতে ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পছন্দ করে, তাই মানুষের জীবনে যখন
কোনো অচেনা বা অনির্দিষ্ট কিছু দেখা দেয়, তখন মন অস্বস্তি অনুভব করে এবং এর ফলে
মানসিক চাপ বাড়ে।
এই অস্বস্তির মূল কারণ হলো মানুষের নিজেকে নিয়ন্ত্রণহীন মনে হওয়া। যখন মস্তিষ্ক
কোনো পরিচিত ধারা বা প্যাটার্ন খুঁজে পায় না, তখন তা আমাদের মনে বিভ্রান্তি ও
দুশ্চিন্তা তৈরি করে। এটা একদম স্বাভাবিক প্রতিক্রিয় হলেও বর্তমানে লোকেদের
জটিল আর ব্যস্ত জীবনে এই অনুভূতি অনেক সময় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় দেখা
দেয়।
কগনিটিভ থিউরি বা চিন্তার মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী অনুযায়ী, জীবনের অনিশ্চিয়তার সময়ে
মানুষ প্রায়ই "ভয়ংকর কল্পনা" বা সর্বনাশা চিন্তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যখন আমরা কোন
পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করতে থাকি এবং সে বিষয়ে আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য না থাকলে,
আমাদের মস্তিস্ক সবচেয়ে খারাপ চিন্তা দিয়ে সে জায়গাটা পূরণ করে। যেমন একজন ছাত্র
যদি পরিক্ষার ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকে, তাহলে কোন কারণ ছাড়াই সে ভাবতে
পারে যে তার ফলাফল খারাপ হবে।
এই ধরনের চিন্তাভাবনা একসময়ে আমাদেরকে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে সাহায্য করত।
কিন্তু আজকের দিনে এসব চিন্তা আমাদের মানসিক চাপ বাড়িয়ে তোলা ছাড়া আর কোন কাজে
আসে না। যেটা এক সময় আমাদের জন্য আত্মরক্ষার উপায় ছিল, সেটাই এখন মানসিক
যন্ত্রনার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো “অনিশ্চয়তা সহ্য করতে না পারা” (Intolerance of Uncertainty বা IU)। এটা এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা, যেখানে কেউ অনিশ্চিত বা অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে খুব বেশি দুশ্চিন্তা ও চাপ অনুভব করে। এই ধরনের মানুষরা অস্বস্তি কমাতে অনেক সময় কোনো বিষয় এড়িয়ে চলে বা ঐ বিষয় নিয়ে আরও বেশি করে তথ্য খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এসব চেষ্টা অনেক সময় উল্টো কাজ করে, এর ফলে ভয় আরও গভীর হয়ে মনের ভেতর গেঁথে যায়।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো “অনিশ্চয়তা সহ্য করতে না পারা” (Intolerance of Uncertainty বা IU)। এটা এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা, যেখানে কেউ অনিশ্চিত বা অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে খুব বেশি দুশ্চিন্তা ও চাপ অনুভব করে। এই ধরনের মানুষরা অস্বস্তি কমাতে অনেক সময় কোনো বিষয় এড়িয়ে চলে বা ঐ বিষয় নিয়ে আরও বেশি করে তথ্য খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এসব চেষ্টা অনেক সময় উল্টো কাজ করে, এর ফলে ভয় আরও গভীর হয়ে মনের ভেতর গেঁথে যায়।
সমাজ ও সংস্কৃতিতে অজানার ভয়ের প্রভাব
অজানার প্রতি ভয় শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটা পুরো সমাজ ও সংস্কৃতিতেও প্রভাব ফেলে।
ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, সামাজিক গোষ্ঠীগুলি অপরিচিত মানুষ, নতুন ধারণা বা
ভিন্ন রীতিনীতির প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে। এই ভয় থেকে অনেক রকম প্রতিক্রিয়া দেখা
যায়ঃ যেমন বিদেশি মানুষকে অপছন্দ করা (জেনোফোবিয়া), বর্ণভিত্তিক বৈষম্য
(বর্ণবাদ), ধর্ম নিয়ে অসহিষ্ণুতা, কিংবা অতিরিক্ত জাতীয় গর্ব (জাতীয়তাবাদ)।
রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংকটের সময় সমাজে ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায়, তখন অনেকেই
অভিবাসী, শরণার্থী বা সংখ্যালঘুদের দায়ী করতে থাকে। তবে এটা তাদের কোনো অপরাধ বা
অসামাজিক কাজের জন্য নয়, বরং তারা নতুন পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার প্রতীক হয়ে ওঠে বলে
মানুষ তাদের ভয় পায়। এসব প্রতিক্রিয়া বেশিরভাগ সময়ই বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়, বরং
সমাজে অজানাকে নিয়ে ভয় ও সন্দেহ থেকেই আসে।
প্রযুক্তির পরিবর্তনও মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা জিন
প্রকৌশলের মতো নতুন উদ্ভাবন ভবিষ্যতে কী প্রভাব ফেলবে, তা না জানার কারণে অনেকেই
শঙ্কিত হন। অনেক সময় সমাজ এসব উন্নয়নের সবদিকগুলোকে ভালোভাবে না বুঝেই অহেতুক
ভয়ের কারণে এদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে বা প্রতিরোধ করতে চায়।
সাংস্কৃতিক কাহিনিগুলো অনেক সময় সমাজের এই সম্মিলিত ভয়েরই প্রতিফলন ঘটায়।
প্রাচীন রুপকথার গল্পগুলোতে অজানার প্রতি ভয়ের প্রতীক হিসেবে বনে-জঙ্গলে, বা
নির্জন জায়গায় লুকিয়ে থাকা ভূত-প্রেত, রাক্ষস, দানব বা এই ধরনের অতিপ্রাকৃতিক
বিপদের কথা বলা হতো । আধুনিক কল্পবিজ্ঞানে পৃথিবীতে ভিনগ্রহের প্রানীদের আক্রমণ
বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভবিষ্যতের চিত্রও একই ধরনের ভয়কে তুলে ধরে।
এই ধরনের গল্প মানুষকে অনিশ্চয়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে এবং তাদেরকে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের অনুভূতিও দেয়। কাহিনির মাধ্যমে ভয়কে যেন এক ধরনের চরিত্র বা রূপ দেওয়া হয়, যাতে সমাজ নিরাপদ দূরত্বে থেকে সেই ভয়কে বুঝে নিতে পারে। ফলে সংস্কৃতি একদিকে আমাদের সম্মিলিত ভয়ের প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে সেই ভয়কে বোঝার একটি মাধ্যমও হয়ে ওঠে।
এই ধরনের গল্প মানুষকে অনিশ্চয়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে এবং তাদেরকে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের অনুভূতিও দেয়। কাহিনির মাধ্যমে ভয়কে যেন এক ধরনের চরিত্র বা রূপ দেওয়া হয়, যাতে সমাজ নিরাপদ দূরত্বে থেকে সেই ভয়কে বুঝে নিতে পারে। ফলে সংস্কৃতি একদিকে আমাদের সম্মিলিত ভয়ের প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে সেই ভয়কে বোঝার একটি মাধ্যমও হয়ে ওঠে।
অজানার ভয় নিয়ে ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি
ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের জীবন ও সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
করে আসছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে ধর্ম অজানার ভয়ের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে
উৎস এবং প্রতিকার হিসেবে কাজ করেছে।
একদিকে, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো (যেমন পরকাল, স্বর্গ-নরক, পাপ ও শাস্তি, কিংবা
অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব ইত্যাদি) মানুষের মধ্যে একধরনের অস্তিত্বগত ভয় তৈরি
করে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অনিশ্চয়তা এবং অদেখা শাস্তির সম্ভাবনা অনেকের মনে
গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কা জাগায়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ধর্মে বিশ্বাস করা হয়, মৃত্যুর পর
আত্মা বিচারের সম্মুখীন হবে, এবং সেই বিচার অনুযায়ী তাকে পুরস্কৃত করা হবে বা
শাস্তি দেওয়া হবে। এই ধরনের ধারণা মৃত্যুকে শুধু একটি জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং এক
অজানা এবং সম্ভাব্য ভীতিকর যাত্রার সূচনা হিসেবে উপস্থাপন করে।
অন্যদিকে, ধর্ম সেই একই অজানার ভয়কে প্রশমিত করার পথও দেখায়। ধর্মীয়
আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, নৈতিক জীবনযাপন বা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এই ভয় থেকে
মুক্তির আশ্বাস দেয়। মানুষের মনের গভীরে থাকা ‘অজানার অন্ধকার’কে ধর্ম অর্থ,
উদ্দেশ্য ও কাঠামোর মধ্যে এনে একধরনের মানসিক আশ্রয় দেয়। এইভাবে, ধর্ম কেবল ভয়
সৃষ্টি করে না, বরং সেই ভয়কে অর্থবহ করে তোলে এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য হিসেবে
উপস্থাপন করে।
শুধু ধর্ম নয়, দর্শনও মানুষের অস্তিত্বগত ভয়, বিশেষ করে অজানার ভয় নিয়ে দীর্ঘদিন
ধরে গভীরভাবে চিন্তা করেছে। বিশেষত, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা এই ভয়কে মানুষের
অভিজ্ঞতার একটি কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে দেখেছেন। জঁ-পল সার্ত্র ও সোরেন
কিয়ের্কেগার্দ এই দুই দার্শনিকের চিন্তায় অজানা, অনিশ্চয়তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা
সম্পর্কিত ভয় একটি মূল থিম হিসেবে কাজ করে এসেছে।
- কিয়ের্কেগার্দ এই অস্তিত্বগত উদ্বেগকে “স্বাধীনতার মাথাঘোরা ভাব” (dizziness of freedom) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, মানুষ যখন বুঝতে পারে যে তার সামনে অসীম সম্ভাবনার দরজা খোলা, সে যা খুশি হতে পারে, যা খুশি করতে পারে,তখন তার মনে এক ধরনের দিশাহীনতা ও ভয় জন্ম নেয়। তার জন্য এই "স্বাধীনতা" কোনো আনন্দের বিষয় নয় বরং গভীর উদ্বেগের উৎস হয়ে দাড়ায়।
- অপরদিকে, সার্ত্র মানুষের অস্তিত্বকে একটি "শূন্য ভিত্তিতে নির্মিত স্বাধীনতা" হিসেবে দেখেছেন। তার মতে, ঈশ্বর বা পূর্বনির্ধারিত কোনও তাৎপর্য না থাকায় মানুষ নিজেই নিজের পরিচয় ও নিজের জীবনের অর্থ গঠন করতে বাধ্য হয়ে থাকে। এই দায়বদ্ধ স্বাধীনতা অর্থাৎ, নিজের জীবন ও সিদ্ধান্তের পূর্ণ দায় নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া মানুষের মনে একটি গভীর অস্তিত্বগত ভয়ের জন্ম দেয়।
অন্যদিকে, বৌদ্ধ ধর্মে অজানার ভয়কে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এখানে অজানাকে নিয়ন্ত্রণ বা ভয় পাওয়ার কিছু নয়, বরং তাকে মেনে নেওয়ার কথা বলা হয়। বৌদ্ধ দর্শনে শেখানো হয় যে, সব কিছুই অনিত্য,অর্থাৎ কোন কিছুই স্থায়ী নয় এবং সব কিছুই বদলায়। তাই আকর্ষণ বা প্রত্যাশার বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে, বর্তমান মুহূর্তে শান্তি খুঁজলেই অজানার ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
সাহিত্য ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে অজানার ভয়
সাহিত্য ও জনপ্রিয় সংস্কৃতি অজানার ভয়কে খুঁজে দেখার ও প্রকাশ করার জন্য এক
দারুণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। গথিক উপন্যাস, ভৌতিক গল্প বা বৈজ্ঞানিক
কল্পকাহিনীগুলোতে অনেক সময় রহস্যময় শক্তি, গোপন সত্য বা নিষিদ্ধ জ্ঞানকে ঘিরে
কাহিনি তৈরি হয়। এসব গল্প পাঠকদের এমন কিছু অনুভব করায়, যা সাধারণভাবে বোঝা কঠিন;
যেখানে পাঠকেরা নিজেদেরকে অজানার মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা পায়।
এই ধারার অন্যতম প্রভাবশালী লেখক ছিলেন এইচ. পি. লাভক্র্যাফট। তিনি তার "কসমিক
হরর" বা মহাজাগতিক আতঙ্কধর্মী রচনার জন্য বিখ্যাত এবং বলেছিলেন, “মানবজাতির
প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ হলো ভয়, এবং সেই ভয়ের প্রাচীনতম ও
শক্তিশালী রূপ হলো অজানার ভয়।” তার গল্পগুলোতে মানুষ এমন সব রহস্যময় ও অজানা
শক্তির মুখোমুখি হয়, যেগুলো তারা বুঝতে পারে না বা তাদের বোঝার ক্ষমতাই মানবজাতির
কল্পনার অতীত। এর ফলে তার গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে অজানাকে নিয়ে এক ধরনের তীব্র
ভয়, বিশাল মহাবিশ্বের কাছে নিজেদের তুচ্ছ হবার অনুভূতি এবং মানসিক ভারসাম্য
হারানোর মতো আতঙ্ক দেখা দেয়।
আধুনিক সিনেমা ও টেলিভিশনেও এই ধারা বজায় আছে। Alien,
The Blair Witch Project কিংবা Interstellar–এর মতো
চলচ্চিত্রগুলোতে চরিত্রদের এমন পরিস্থিতিতে দেখা যায়, যেখানে চারপাশ ঘিরে থাকে
অজানা ও নিয়ন্ত্রণহীন ভয়। এমনকি রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনিগুলোও মূলত অজানাকে জানার
চেষ্টা নিয়ে গড়ে ওঠে, যা মানুষের ভেতরের জানার আগ্রহ ও কৌতূহলকে তুলে ধরে।
এ ধরনের কাহিনীগুলো আমাদের মানসিকতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। মানুষ যখন
ভয়ের গল্প পড়ে বা সিনেমা দেখে, তখন সে বাস্তব জীবনের ভয়গুলোকে
নিরাপদভাবে অনুভব করতে পারে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ভয়, আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলার
মুখোমুখি হয়ে আমরা আমদের মনে চেপে রাখা দুশ্চিন্তাগুলো থেকে মানসিক মুক্তি বা
ক্যাথারসিস লাভ করতে পারি।
অন্যদের ভয় পেতে দেখলে দর্শক নিজের ভয়গুলোও সাহস করে অনুভব করতে পারে। এভাবে
সাহিত্য ও গণমাধ্যম আমাদের ভয়ের ছবি তুলে ধরে এবং সেই ভয় মোকাবেলার একটা উপায়
হয়ে ওঠে।
অজানার ভয় নিয়ে গনমাধ্যমের ভূমিকা
বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে গণমাধ্যম অজানার ভয় নিয়ে মানুষের মনে মিশ্র
প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। একদিকে যেমন এটি সঠিক তথ্য দিয়ে মানুষকে আশ্বস্ত
করতে পারে, অন্যদিকে ভুল বা বিভ্রান্তিকর খবর দিয়ে মানুষের মাঝে আতঙ্ক বাড়িয়ে
তুলতেও পারে। এই দুই ধরনের প্রভাব আধুনিক যুগে গণমাধ্যমকে মানুষের আবেগ ও
প্রতিক্রিয়া গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছে।
ইতিবাচক দিক থেকে দেখলে, সঠিক ও সহজলভ্য তথ্য মানুষের অনিশ্চয়তা কমিয়ে
আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন, জনস্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতামূলক
প্রচারাভিযান মানুষকে রোগ নিয়ে ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করে এবং রোগকে সঠিকভাবে
মোকাবেলা করার জন্য জনগনকে কার্যকর নির্দেশনা দেয়। ফলে সঠিক তথ্য জানলে মানুষ
বেশি শান্ত থাকে এবং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনা করে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে
পারে।
তবে গণমাধ্যম কখনও কখনও অতিরঞ্জিত বা ভুল তথ্য প্রচার করে কখনও কখনও ভয় আরও
বাড়িয়ে তুলতে পারে। ভয়ঙ্কর শিরোনাম, ষড়যন্ত্রমূলক তত্ত্ব কিংবা যাচাই না করা
দাবি মানুষের মনে বাস্তবকে নিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক একটি ছবি এঁকে
দেয়। এই ধরনের কনটেন্ট অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে মানুষের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও
আতঙ্ক সৃষ্টি করে যাতে করে তাদের ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে
অনেকে বেশি ভিউ আসে।
সংকটের সময় গণমাধ্যমের প্রভাব আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতিতে যদি পরিষ্কার ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য না মেলে, তাহলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর ফলে তাদেরকে অনেক সময় হুট করে কেনাকাটা, অন্যদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ কিংবা সরকারি নির্দেশ না মানার মতো অযৌক্তিক আচরণ করতে দেখা যায়। যখন অনিশ্চয়তা বেড়ে যায়, তখনই ভয়ের জন্ম হয়, আর সেই ভয় মানুষকে ভুল পথে চালিত করতে পারে।
সংকটের সময় গণমাধ্যমের প্রভাব আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতিতে যদি পরিষ্কার ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য না মেলে, তাহলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর ফলে তাদেরকে অনেক সময় হুট করে কেনাকাটা, অন্যদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ কিংবা সরকারি নির্দেশ না মানার মতো অযৌক্তিক আচরণ করতে দেখা যায়। যখন অনিশ্চয়তা বেড়ে যায়, তখনই ভয়ের জন্ম হয়, আর সেই ভয় মানুষকে ভুল পথে চালিত করতে পারে।
তাই বর্তমান যুগে সরকারকে শুধু সংকট সামাল দিলেই চলবে না, বরং মানুষের মনে অজানার
ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গণমাধ্যমের আসল দায়িত্ব হলো
মানুষের মাঝে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া, তাদের মনে আতঙ্ক ছড়ানো নয়। আজকের সংযুক্ত
বিশ্বে তথ্য কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেটাই ঠিক করে দেয় সমাজ শান্ত থাকবে, না
কি বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে।
অজানার ভয়কে জয় করার উপায়
অজানার প্রতি ভয় মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলেও, সেটি এমন হওয়া উচিত নয়
যা মানুষকে দুর্বল বা স্থবির করে দেয়। মানুষ চাইলে এই ভয়কে
স্বাস্থ্যকর ও গঠনমূলকভাবে মোকাবিলা করতে শিখতে পারে। সঠিক কৌশল গ্রহণ করলে
অজানার ভয়কে শুধু কাটানোই যায় না, বরং তাতে আত্মবিশ্বাস, মানসিক শক্তি ও
ব্যক্তিগত বিকাশও ঘটে।
অজানার ভয়কে জয় করার একটি কার্যকর উপায় হলো মানসিক সহনশীলতা তৈরি করা।
মাইন্ডফুলনেস অনুশীলন, থেরাপি বা আধ্যাত্মিক চর্চা মানুষকে শেখায় কীভাবে
অনিশ্চয়তার মধ্যেও স্থির থাকতে হয়। দ্রুত সমাধানের খোঁজে না গিয়ে অস্বস্তির
মধ্যে ধৈর্য ধরে থাকার অভ্যাসই ধীরে ধীরে আমাদের মনকে ভয়কে মোকাবেলা করার জন্য যে
গভীর মানসিক শক্তি দরকার তাকে গড়ে তোলে।
ভয় কাটিয়ে ওঠার পথে শিক্ষা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। যখন
মানুষ বিজ্ঞান, ইতিহাস কিংবা সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন অজানা বিষয়গুলো
আর ততটা ভীতিকর মনে হয় না। জ্ঞান মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে, আর কৌতূহল ভয়ের
জায়গায় সাহস ও অনুসন্ধিৎসা জন্ম দেয়। সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ
আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে না থাকলেও, এই
জানতে চাওয়ার শক্তিই আমাদের ভয়কে জয় করতে শেখায়।
অপরিচিত বিষয়ের মুখোমুখি হতে গেলে উদার ও মানিয়ে চলার মতো মানসিকতা থাকা খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। মনোবিজ্ঞানী ক্যারল ডুয়েকের “গ্রোথ মাইন্ডসেট” ধারণা অনুযায়ী,
নতুন ও অজানা অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের জন্যে হুমকি না হয়ে বরং তা আমাদেরকে নতুন কিছু
শেখার সুযোগ করে দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে চ্যালেঞ্জ থেকে পালানোর বদলে তা
সাদরে গ্রহণ করতে শেখায়। ফলে অজানাকে ভয়ের জায়গায় না দেখে, একজন অনুসন্ধানীর
দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়।
সমষ্টিগতভাবে সমাজও এই ভয় কমাতে সাহায্য করতে পারে। একে অপরের খোলামেলা
যোগাযোগ, সমাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব
মানুষের মনে নিরাপত্তার অনুভূতি জাগায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ
বা বিপদের সময় যদি নেতারা স্পষ্ট বার্তা দেন এবং শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা
করেন, তখন মানুষ আস্থা পায় ও স্থির থাকতে পারে।
শেষ কথা
পরিশেষে বলা যায়, অজানার ভয় আমাদের সবার ভেতরেই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। এটা
শুধু একটা অনুভূতি নয়, বরং এটি আমাদের বিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক প্রাচীন
প্রবৃত্তি, যেটা আজও আমাদের ভাবনা, অনুভব ও আচরণে ছাপ ফেলে।
অজানার ভয় আমাদের পেছনে টেনে ধরতে পারে, কিন্তু ঠিক সেই ভয়ই আমাদের সামনে
এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণাও হতে পারে। ভয়কে স্বীকার করে তার মুখোমুখি দাঁড়ালে,
মানুষ এবং সমাজ উভয়ই এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আরও বেশি সহনশীল, বুদ্ধিমান
ও দয়ালু হয়ে উঠতে পারে।
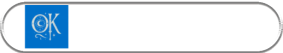








অতিপ্রাকৃতিক ব্লগের নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url