অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাগুলো যেভাবে প্রকাশ পায়
আমাদের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে থাকা অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাগুলো যুগ
যুগ ধরে মানবজাতিকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে আসছে। প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতিষী থেকে
শুরু করে আধুনিক যুগের টেলিভিশনের ভবিষ্যদ্বক্তা পর্যন্ত, মানুষের মনে এর আকর্ষণ
কখনও কমে যায়নি।
এই প্রবন্ধে নানা ধরনের অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতা ও তাদের সাংস্কৃতিক শিকড়
অনুসন্ধান করা হয়েছে; এর পাশাপাশি ইতিহাসের নানা পর্যায়ে পাওয়া উল্লেখযোগ্য
উদাহরণগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতা
নিয়ে বিশ্বাস ও সংশয়ের চলমান বিতর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যেই বিতর্ক আজও
মানুষকে একইসঙ্গে মুগ্ধ করে এবং বিভক্ত করে রাখে।
সূচিপত্রঃ অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাগুলো যেভাবে প্রকাশ পায়
- টেলিপ্যাথিঃ মনের সাথে মনের সরাসরি যোগাযোগ
- ক্লেয়ারভয়েন্সঃ দৃশ্যমান জগতের সীমা ছাড়িয়ে দেখতে পারার ক্ষমতা
- প্রিকগনিশনঃ ভবিষ্যতের আভাস দেখা
- সাইকোকাইনেসিসঃ মনের শক্তিতে বস্তু নিয়ন্ত্রণ করা
- মিডিয়ামশিপঃ মৃতদের সাথে যোগাযোগ করা
- অরা রিডিংঃ জীবন্ত সত্তার চারপাশে থাকা অদৃশ্য শক্তিক্ষেত্রকে দেখা বা অনুভব করা
- অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশনঃ দেহের বাইরে ভ্রমণ
- সাইকোমেট্রিঃ স্পর্শের মাধ্যমে জানা
- অ্যানিমেল টেলিপ্যাথিঃ প্রাণীদের সঙ্গে মনের যোগাযোগ
- সাইকিক হিলিংঃ মানসিক শক্তি ব্যবহার করে রোগীকে সারিয়ে তোলা
- শেষ কথা
টেলিপ্যাথিঃ মনের সাথে মনের সরাসরি যোগাযোগ
টেলিপ্যাথি হলো এক রহস্যময় ক্ষমতা, যেখানে কোনো শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা প্রযুক্তি
ব্যবহার না করেই একজনের চিন্তা, অনুভূতি বা কল্পনা করা ছবি সরাসরি অন্যের মনের
কাছে পৌঁছে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাটি যেমন
বিশ্বাসীদের মুগ্ধ করেছে, তেমনি সংশয়বাদীদের মনেও কৌতূহল জাগিয়েছে; যার ফলে এই
ক্ষমতাটি মিথ, কিংবদন্তি ও দার্শনিক রচনায় বারবার স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ একে
নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেও, অনেকেই মনে করেন এটি মানুষের অদৃশ্য মানসিক
সম্ভাবনারই এক ঝলক, যা এখনও পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি।
প্রাচীন ভারতে যোগ সাধনায় মনঃসম্বাদ নামে পরিচিত এক বিশেষ ধরনের মানসিক
যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে, যাকে গভীর ধ্যান ও একাগ্রতার মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব
বলে মনে করা হতো। যোগীদের বিশ্বাস ছিল, মন যদি জাগতিক আসক্তি ও বিভ্রান্তি থেকে
মুক্ত হয়, তবে তা শারীরিক সীমাবদ্ধতাকেও অতিক্রম করতে পারে। এসব আমাদেরকে ইঙ্গিত
দেয় যে টেলিপ্যাথি কেবল কল্পকাহিনি নয়, বরং আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ ও মানসিক
শক্তির এক শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ।
উনিশ শতকে পাশ্চাত্য বিশ্বে
আত্মিকতাবাদীরা
দাবি করেছিলেন যে সিয়াঁস অনুষ্ঠানের (Séance,
এক ধরনের অনুষ্ঠান যেখানে একজন বিশেষ ব্যাক্তির, যাকে মিডিয়াম বলা হয়, মাধ্যমে
মৃত ব্যাক্তিদের আত্মাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়) মাধ্যমে টেলিপ্যাথি প্রদর্শন করা সম্ভব। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অনেক মিডিয়াম
দাবী করতেন যে তারা অংশগ্রহণকারীদের মনের গোপন ভাবনা জানতে পারছেন কিংবা এই জগতের
বাইরের আত্মাদের কাছ থেকে বার্তা পাচ্ছেন। রহস্যময় বিনোদন আর অদৃশ্য জগতের সঙ্গে
যোগাযোগের আশা একসাথে মিশে যাবার কারনে এই ধরনের দাবি সেই সময়ের ইউরোপ, আমেরিকার
সাধারন জনগণদেরকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।
বিশ শতকে প্যারাসাইকোলজিস্ট জে. বি. রাইনের উদ্যোগে টেলিপ্যাথি নিয়ে বৈজ্ঞানিক
অনুসন্ধানের চেষ্টা শুরু হয়। ১৯৩০-এর দশকে তিনি “অতিরিক্ত সংবেদনশীল উপলব্ধি”
(ESP) যাচাই করার জন্য বিশেষ ধরনের কার্ড ব্যবহার করে পরীক্ষা চালান। কিছু
ক্ষেত্রে ফলাফলকে পরিসংখ্যানগতভাবে অস্বাভাবিক মনে হলেও, সমালোচকদের মতে এগুলো
কেবল কাকতালীয় ঘটনা অথবা গবেষণার নকশাগত ত্রুটির ফলাফল ছাড়া আর কিছু নয়।
বৈজ্ঞানিক মহলে সংশয় থাকলেও টেলিপ্যাথি এখনো গবেষক ও সাধারণ মানুষের কাছে
কৌতূহলের বিষয় রয়ে গেছে। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের কিছু গবেষনায় পরীক্ষা করে দেখা
হচ্ছে প্রযুক্তির সাহায্যে মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব
হতে পারে কি না। যদিও এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রকৃত টেলিপ্যাথির সংজ্ঞায় পড়ে না,
তবুও এসব পরীক্ষা মানব মনের অদৃশ্য ক্ষমতা নিয়ে আলোচনাকে আজও প্রাণবন্ত ও
প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।
ক্লেয়ারভয়েন্সঃ দৃশ্যমান জগতের সীমা ছাড়িয়ে দেখতে পারার ক্ষমতা
ক্লেয়ারভয়েন্স (Clairvoyance) হলো এমন একটি অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতা, যার
মাধ্যমে সাধারণ ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে বস্তু বা ঘটনাকে উপলব্ধি করা সম্ভব
বলে মনে করা হয়। এটি কখনও বর্তমানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিছু দেখার সঙ্গে, কখনও
অতীতের দৃশ্য জানার কিংবা ভবিষ্যতের আভাস পাওয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে।
ক্লেয়ারভয়েন্স শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ “পরিষ্কারভাবে
দেখা,” আর সেটিই এই রহস্যময় ক্ষমতার আসল ধারনাকে প্রকাশ করে।
ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এই অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাটি নানা সংস্কৃতি ও
কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। মধ্যযুগের জ্যোতিষীরা দাবি করতেন যে
তারা দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য কিংবা গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ
করতে পারেন। আবার আদিবাসী সমাজের শামানরা তন্ময় অবস্থায় এমন সব দর্শনের
অভিজ্ঞতার কথা বলতেন, যা দূরবর্তী ঘটনার আভাস দিত বা গভীর আধ্যাত্মিক সত্য
উন্মোচিত করত।
আধুনিক যুগেও, বিশেষ করে বিংশ শতকে, ক্লেয়ারভয়েন্স নিয়ে মানুষের কৌতূহল অটুট
ছিল। এর সবচেয়ে আলোচিত দৃষ্টান্ত হলো আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ (CIA) এর
প্রজেক্ট স্টারগেইট , যেখানে “রিমোট ভিউইং” (পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী "ভিউয়ার"দের বলা হতো চোখ বন্ধ করে বা ধ্যানমগ্ন
অবস্থায় দূরের কোনো গোপন স্থাপনা, শত্রুপক্ষের ঘাঁটি বা নথি কেমন দেখতে তা
বর্ণনা করতে। গবেষকরা যাচাই করতেন সেই বর্ণনা বাস্তবের সঙ্গে মেলে কি না।) পরীক্ষা চালানোর জন্য বিশেষভাবে অর্থায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল
ক্লেয়ারভয়েন্স ক্ষমতাকে কি সত্যিই গুপ্তচরবৃত্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো
বাস্তব কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে কি না তা খতিয়ে দেখা।
এসব পরীক্ষায় অংশগ্রহন করা কেউ কেউ গোপন বস্তু বা অদৃশ্য স্থানের এমন বর্ণনা
দিয়েছিলেন, যা আশ্চর্যজনকভাবে বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায়। এসব ঘটনা একদিকে
জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িয়েছিল, অন্যদিকে সরকারি গবেষণাকেও উৎসাহিত করেছিল। তবে
সামগ্রিকভাবে ফলাফল ধারাবাহিক না হওয়ায় ক্লেয়ারভয়েন্সকে নির্ভরযোগ্য বা
বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায়নি।
সংশয়বাদীরা মনে করেন, ক্লেয়ারভয়েন্ট অভিজ্ঞতা প্রায়ই কাকতালীয় মিল, অবচেতন
মনের বিশ্লেষণ অথবা নিছক দক্ষ অনুমানের ফল হতে পারে। বিজ্ঞানীরা জোর দিয়ে বলেন
যে কঠোর ও নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার পরিবেশে সাধারণত এই ক্ষমতাকে নির্ভরযোগ্যভাবে
প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। সেই কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের কৌতূহল
জাগিয়েও মূলধারার বিজ্ঞান ক্লেয়ারভয়েন্সকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি।
তারপরেও আধুনিক জ্যোতিষচর্চায় ক্লেয়ারভয়েন্স স্বচ্ছন্দে নিজের জায়গা করে
নিয়েছে। অনেক অনুশীলনকারী দাবি করেন, তারা নাকি ক্লায়েন্টদের জীবনপথ, সম্পর্ক
কিংবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গোপন সত্য প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং বাস্তব বা নিছক
কল্পনা যাই হোক না কেন, ক্লেয়ারভয়েন্স এখনো মানব কল্পনার জগতে এক চিরন্তন
আকর্ষণ হয়ে টিকে আছে।
প্রিকগনিশনঃ ভবিষ্যতের আভাস দেখা
প্রিকগনিশন (Precognition) , বা ভবিষ্যৎ দর্শন, হলো সবচেয়ে বেশি আলোচিত
অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাগুলির মধ্যে একটি। এই ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যতের
ঘটনা ঘটার আগেই তার আভাস পেতে পারে; যা কখনও স্বপ্নে, কখনও দর্শনে বা হঠাৎ উদ্ভূত
অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অনেকের কাছে এটি বর্তমানের সঙ্গে অজানা
ভবিষ্যতের সম্ভাবনার এক রহস্যময় সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
বিশ্বের নানা ধর্মীয় ঐতিহ্যে প্রিকগনিশন সম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের উল্লেখ পাওয়া
যায়। বাইবেল ও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নবীগণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঐশ্বরিক দর্শন লাভ
করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এসব ধর্মগ্রন্থে এই দর্শনগুলোকে কখনও
দিকনির্দেশনা, কখনও সতর্কবার্তা, আবার কখনও উচ্চতর শক্তির উপস্থিতি ও প্রমাণ
হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে প্রাচীন সংস্কৃতিতেও ভবিষ্যৎদর্শী ব্যক্তিদের প্রতি
গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন গ্রিসে
ডেলফির ওরাকল
যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক পরিকল্পনা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণের আগে পরামর্শ
দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব প্রথা স্পষ্ট করে যে প্রাচীন সমাজগুলোতে
ভবিষ্যৎজ্ঞানকে অমূল্য সম্পদ মনে করা হতো এবং তা প্রায়শই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
ইতিহাসের সাম্প্রতিক সময়েও প্রিকগনিশন অসংখ্য কাহিনি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়
প্রকাশ পেয়েছে। বহু মানুষ দাবি করেছেন যে তারা আগেভাগেই স্বপ্নে জাহাজডুবি,
ভূমিকম্প বা ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য দেখেছিলেন। নিছক কাকতালীয় ঘটনা
বা সত্যিকারের ভবিষ্যৎদর্শন যাই হোক না কেন, এসব ঘটনা মানব মনের অজানা ক্ষমতা
নিয়ে আজও আমাদের কৌতূহল ও বিস্ময় জাগিয়ে তোলে।
তবে বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদীরা এসব দাবিকে সরাসরি গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন। তাদের
মতে, প্রিকগনিশনের অভিজ্ঞতা অনেক সময় কাকতালীয় ঘটনা, বাছাই করা স্মৃতি বা
অবচেতনভাবে ধরা পড়া কোনো প্যাটার্নের ফল হতে পারে। নিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক
পরীক্ষায় এখনো ভবিষ্যৎ দর্শনের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি।
সাইকোকাইনেসিসঃ মনের শক্তিতে বস্তু নিয়ন্ত্রণ করা
সাইকোকাইনেসিস (Psychokinesis), যাকে প্রায়ই টেলিকাইনেসিসও বলা , হলো এক ধরনের
কথিত ক্ষমতা যেখানে শুধুমাত্র মনের শক্তি দিয়ে ভৌত বস্তুতে প্রভাব ফেলা যায়। এই
অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতার মাধ্যমে কেউ শারীরিকভাবে স্পর্শ বা সরাসরি যোগাযোগ
ছাড়াই মানসিক শক্তির মাধ্যমে তার আশেপাশের পরিবেশ বা পদার্থে পরিবর্তন ঘটাতে
পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ধারণাটি মানুষের মনে কৌতূহল জাগিয়েছে এবং তা
অতিপ্রাকৃত নিয়ে গবেষণা থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির
অন্যতম আকর্ষণীয় উপাদান হয়ে উঠেছে।
ইতিহাস জুড়ে সাইকোকাইনেসিসের মতো ক্ষমতার আভাস বহনকারী ব্যাক্তিদের নিয়ে বহু
কিংবদন্তি ও লোককাহিনি প্রচলিত রয়েছে। রহস্যময় সাধক ও শামানদের নিয়ে বলা হতো,
তারা আচার-অনুষ্ঠানের সময় কেবল মানসিক শক্তি দিয়ে বস্তু নাড়াতে পারতেন, যা
তাদের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও প্রভাবকে তুলে ধরত। এসব কাহিনীকে মূলত লোককথা হিসেবে
ধরা হলেও সেগুলো মনের শক্তি দিয়ে বাস্তবকে জয় করার ধারণার প্রতি মানুষের
আকর্ষণকে আরও গভীর করেছে।
আধুনিক যুগে কিছু আলোচিত ব্যক্তিত্বের হাত ধরে সাইকোকাইনেসিস সাধারণ মানুষের
আলোচনায় আসে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭০-এর দশকে
উরি গেলার
সরাসরি টেলিভিশনে চামচ বাঁকানোসহ নানা রকম অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের করে
সেই সময়ের জনগনের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলেন। তবে তার এসব কর্মকাণ্ডকে ঘিরে
তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়; কেউ একে সত্যিকারের অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতা বলে
মানতেন, আবার অনেকেই একে নিছক কৌশল বা প্রতারণা বলে মনে করতেন।
গবেষকরাও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সাইকোকাইনেসিস নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা
চালিয়েছেন। অংশগ্রহণকারীদেরকে কখনও পাশা ফেলার ফলাফল পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে,
কখনও র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটরের ধারা প্রভাবিত করতে, আবার কখনও ছোট ধাতব বল বা
সূক্ষ্ম বস্তুর গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হয়েছে। কিছু পরীক্ষায়
পরিসংখ্যানগতভাবে অস্বাভাবিক ফলাফল ধরা পড়লেও তা ধারাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্তি করা
যায়নি।
সংশয়বাদীদের মতে, সাইকোকাইনেসিস কখনোই কঠোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্যভাবে
প্রমাণিত হয়নি। কথিত অনেক ঘটনাই আসলে হাতের কৌশল, পরীক্ষার নকশাগত ত্রুটি, কিংবা
এলোমেলো ঘটনায় প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়ার মানবিক প্রবণতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা
সম্ভব। সেই কারণেই মূলধারার বিজ্ঞান এখনো এর অস্তিত্ব নিয়ে স্পষ্টতই সংশয়ী
অবস্থান ধরে রেখেছে।
মিডিয়ামশিপঃ মৃতদের সাথে যোগাযোগ করা
মিডিয়ামরা দাবি করেন যে তারা জীবিতদের সঙ্গে মৃত ব্যাক্তিদের আত্মাদের মধ্যে
সেতুবন্ধনের কাজ করেন। তাদের কাজ হলো পরলোক থেকে জীবিতদের মধ্যে বার্তা পৌঁছে
দিয়ে এই দুই জগতের মধ্যে একধরনের সম্পর্ক ও উপস্থিতির অনুভূতি তৈরি করা। এই
বিশ্বাস ইতিহাস জুড়ে নানা সংস্কৃতিতে মানুষের মধ্যে বিস্ময়, আশা এবং সান্ত্বনার
উৎস হয়ে এসেছে।
উনিশ শতকের স্পিরিচুয়ালিস্ট আন্দোলনের সময় মিডিয়ামশিপ এক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা
লাভ করে। সেই সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় সিয়াঁস কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনই ছিল না,
বরং তা সামাজিক সমাবেশের রূপ নেয়। সেসব অনুষ্ঠাণে মানুষ তাদের প্রিয়জনের আত্মার
কাছ থেকে সংবাদ বা সান্ত্বনা পাওয়ার আশায় যোগদান করত। মৃতদের সঙ্গে সরাসরি
কথোপকথনের এই প্রতিশ্রুতিই স্পিরিচুয়ালিজমকে একদিকে ধর্মীয় বিশ্বাসের, আরেকদিকে
আবেগময় সংযোগের গভীর আকর্ষণ প্রদান করেছিল।
মিডিয়ামরা মৃত ব্যাক্তিদের আত্মাদের বার্তা তাদের প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছানোর জন্য
বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। বেশিরভাগ মিডিয়ামরা অনুষ্ঠান চলাকালে গভীর
ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রবেশ করেন, যেখানে বিশ্বাস করা হয় আত্মা তাদের দেহ ও কণ্ঠ
ব্যবহার করে কথা বলে। অন্যরা চোখ বন্ধ করে কাগজে কলমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন করে
লিখতে থাকেন যেন মনে হয় অদৃশ্য কোনো শক্তি তাদের হাতকে চালিত করছে। আবার
কেউ অন্ধকার ঘরে সিয়াঁসের আয়োজন করেন, যাতে পরিবেশ আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে এবং
অংশগ্রহণকারীরা তাদের চারিপাশে আত্মাদের অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন।
মিডিয়ামশিপের ইতিহাসে অন্যতম আলোচিত নাম হলো নিউ ইয়র্কের
ফক্স সিস্টার্স। নিউ ইয়র্কের এই তিন বোনের তৈরি রহস্যময় ঠকঠক শব্দ প্রথমে আত্মার
সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়েছিল এবং তাদেরকে আমেরিকান
স্পিরিচুয়ালিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ মনে করা হয়। কিন্তু বহু বছর পর তারা স্বীকার
করেন যে শব্দগুলো তাদেরই তৈরি এক কৌশল ছিল, যা তাদের আসল দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ
করে তোলে এবং পুরো আন্দোলনকে বিতর্কিত করে।
এই তিন বোনের এবং তার পরেও অনেক লোকের ধোঁকাবাজি ধরা পড়া স্বত্তেও মিডিয়ামশিপের
জনপ্রিয়তা কমে যায়নি। পরবর্তীতে আরও বহু মিডিয়াম ব্যক্তিগতভাবে বা জনসমক্ষে মৃত
মানুষের আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আপাতদৃষ্টিতে তাদের অতিপ্রাকৃতিক
মানসিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে,
মানুষের মধ্যে সান্ত্বনা ও আশার আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই সংশয় বা শঙ্কার চেয়ে অনেক
শক্তিশালী হয়ে থাকে।
সংশয়বাদীরা মনে করেন, মিডিয়ামশিপ মূলত মনস্তাত্ত্বিক কৌশল যেমন
কোল্ড রিডিং-এর ওপর নির্ভর করে, যেখানে সাধারণ ও অস্পষ্ট কথাকে ব্যক্তিগত বার্তার মতো মনে
হয়। তারা আরও বলেন, শোকগ্রস্ত মানুষদের আবেগীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত
মিডিয়ামরা অসহায় মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা মেরে খায়। তাই
অনেকের দৃষ্টিতে মিডিয়ামশিপ প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধনার বদলে মূলত এক ধরনের অভিনয়
মাত্র।
অরা রিডিংঃ জীবন্ত সত্তার চারপাশে থাকা অদৃশ্য শক্তিক্ষেত্রকে দেখা বা অনুভব করা
নিজেদের অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করা কেউ কেউ দাবী করেন যে তারা
জীবিত প্রাণীর চারপাশে থাকা একধরনের অদৃশ্য ও সূক্ষ্ণ শক্তিক্ষেত্রকে, যাকে অরা
(Aura) বলা হয়, দেখতে ও অনুভব করতে পারেন। তাদের মতে, এই অরা দেহের বাইরে রঙিন
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং তা মানুষের মনের ভেতরের অবস্থা ফুটিয়ে তোলে।
অনুশীলনকারীদের মতে, এই আভা একজনের আবেগ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে
প্রতিফলিত করে।
এই আভা বা অরার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়শই নানা রঙের উল্লেখ করা হয়, যেখানে
প্রতিটি রঙের সঙ্গে একটি বিশেষ তাৎপর্য জড়িয়ে থাকে। উদাহরন স্বরূপ, নীলকে
শান্তি ও প্রশান্তির প্রতীক ধরা হয়, লালকে আবেগ, শক্তি ও তীব্র অনুভূতির সঙ্গে
যুক্ত করা হয়। অন্যদিকে সোনালি রঙকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা উচ্চতর প্রজ্ঞার চিহ্ন
হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
অনেক সংস্কৃতিতে আভাকে আলাদা কোনো ধারণা হিসেবে নয়, বরং বৃহত্তর আধ্যাত্মিক
ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে
চক্র
বা শক্তিকেন্দ্রের মাধ্যমে একই ধরনের ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দেহ ও মনের
ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা হয়।একইভাবে, চীনা
চিকিৎসাশাস্ত্রে
চি
বা জীবনশক্তির গুরুত্বে জোর দেওয়া হয়েছে, যা দেহকে সুস্থ ও স্থিতিশীল রাখে বলে
বিশ্বাস করা হয়।
বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যকার এই মিলগুলি প্রমান করে যে ইতিহাস জুড়েই মানুষ তাদের
দৈনদিন জীবনে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবকে বোঝার চেষ্টা করেছে। আভা, চক্র ও চি-এসব
ধারণাগুলো আসলে দেহ, মন ও আত্মার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার উপায়। বাস্তব শক্তি বা
প্রতীকী রূপে যেভাবেই ধরা হোক না কেন, এগুলো মানুষের অভিজ্ঞতাকে ভৌত
বাস্তবতার গণ্ডির বাইরে ব্যাখ্যা করার একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।
কিন্তু এখনো পর্যন্ত আভার অস্তিত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলেনি। গবেষকরা মনে
করেন, আভা দেখার অভিজ্ঞতা মূলত কল্পনা, প্রস্তাবনা কিংবা অতিসংবেদনশীল অনুভূতির
মতো মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। সেই কারণে সংশয়বাদীরা আভা-পাঠকে
অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতার কোন নিরপেক্ষ প্রমাণ নয়, বরং ব্যক্তিগত
অনুভূতি বলে মনে করেন।
তবুও আধুনিক যুগে এসেও এই রহস্যময় অরা বা শক্তি ক্ষেত্রগুলোকে ধরতে নান রকম
যন্ত্রের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরন স্বরূপ,
কিরলিয়ান ফটোগ্রাফি
কোনো বস্তুর চারপাশে আলোকোজ্জ্বল ছবি তুলে ধরে, যাকে অনেকে আভার দৃশ্যমান প্রকাশ
হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তবে মূলধারার বিজ্ঞান এ ছবিগুলোকে দেহ বা বস্তুর মধ্য নিয়ে
স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক নির্গমনের ফলাফল বলেই মনে করে; আর আধ্যাত্মিক চর্চাকারীরা
এগুলোকে জীবন্ত সত্তার চারপাশে বজায় থাকা শক্তিক্ষেত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ
হিসেবে দেখেন।
অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশনঃ দেহের বাইরে ভ্রমণ
অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশন (Astral Projection), যাকে আউট-অফ-বডি এক্সপেরিয়েন্স (OBE)
ও বলা হয়, মূলত দেহ থেকে চেতনার সাময়িক সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতিকে
বোঝায়। এ অভিজ্ঞতার দাবি করা অনেকেই বলেন, তারা যেন দেহের শারীরিক সীমা ছাড়িয়ে
অন্য কোথাও বা এমনকি আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণ করে এসেছেন। অনেকেই এই অতিপ্রাকৃতিক
মানসিক ক্ষমতাকে নিজেদের চেতনাকে ব্যবহার করে এই মহাবিশ্বের রহস্যগুলোকে গভীরভাবে
অনুসন্ধানের একটি অনন্য পথ হিসেবে দেখেন।
বিশ্বের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এ ধরনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়।
প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন
কা
নামের এক আত্মিক সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, যা দেহের বাইরে গিয়ে ভ্রমণ করতে পারে।
আবার তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের সাধনায়, বিশেষত
ড্রিম ইয়োগায়, অনুশীলনকারীরা ঘুমের ভেতরেই সচেতনভাবে আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণের চেষ্টা
করেন।
আধুনিক যুগে অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশনের অভিজ্ঞতার বর্ণনাগুলোও আশ্চর্যজনকভাবে একে
অপরের সঙ্গে মিলে যায়। অনেকে জানান, তারা যেন নিজের দেহের ওপরে ভেসে উঠেছে এবং
ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে। আবার কেউ কেউ দাবি করেন, তারা
দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করেছেন কিংবা অশরীরী সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।
কিছু অনুশীলনকারীদের মতে, অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশন ধ্যান ও গভীর মানসিক প্রশান্তির
সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তারা বিশ্বাস করে যে মনকে সম্পূর্ণ শান্ত করতে পারলে
আত্মাকে দেহের শারীরিক বন্ধন থেকে সচেতনভাবে সাময়িক সময়ের জন্য মুক্ত করা যায়।
তারা মনে করেন যে বিশেষ কিছু কৌশল ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই ক্ষমতাকে সহজভাবে
আয়ত্ত্ব করা সম্ভব।
তবে বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাদের গবেষণা মতে,
অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশন মূলত মস্তিষ্কের কিছু বিশেষ কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত, যা
প্রায়ই স্লিপ প্যারালাইসিস কিংবা মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থায় (Near Death
Experience) গেলে মানুষ অনুভব করে থাকে। বৈজ্ঞানিকভাবে তাই এটি কোনো বাস্তব ভ্রমণ
নয়; বরং মনের ভেতরের অভিজ্ঞতা ও স্নায়বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারই প্রতিফলন
মাত্র।
তবুও নানা ধরনের সংশয় থাকা সত্ত্বেও অ্যাস্ট্রাল প্রজেকশন আধ্যাত্মিক
অনুসন্ধানীদের কাছে এখনো একটি রহস্যময় কৌতূহলের উৎস হয়ে আছে। অ্যাস্ট্রাল
প্রজেকশনের অভিজ্ঞতার দাবি করা অনেকেই বলেন, এতে তারা এক ধরনের অসীম স্বাধীনতা,
মানসিক স্বচ্ছতা এবং বাস্তবতার প্রকৃতি নিয়ে গভীর উপলব্ধি লাভ করেন। এই
শক্তিশালী অভিজ্ঞতাগুলোই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ অটুট
রেখেছে।
সাইকোমেট্রিঃ স্পর্শের মাধ্যমে জানা
সাইকোমেট্রি (Psychometry) এমন একধরনের অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতা যেখানে একজন
ব্যক্তি কোন বস্তু বা মানুষকে স্পর্শ করেই তার সম্পর্কে নানারকম তথ্য জানতে পারে।
এরকম ক্ষমতার দাবী করা ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে শারীরিক সংস্পর্শের মাধ্যমে তারা
এমন সব গোপন বিষয় অনুভব করতে পারেন যা সাধারণভাবে ধরা যায় না। এসব অনুভূতির
মধ্যে আবেগ, ব্যক্তিগত স্মৃতি এমনকি অতীত ঘটনার ঝলকও থাকতে পারে।
সাইকোমেট্রির সমর্থকদের মতে, প্রতিটি বস্তু আসলে এক ধরনের "স্মৃতিরক্ষক" হিসেবে
কাজ করে। তাদের ধারনা অনুযায়ী জিনিসপত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মালিকের শক্তি শোষণ
করে এবং অভিজ্ঞতার ছাপ নিজের ভেতরে জমা করে রাখে। কোনো সংবেদনশীল ব্যক্তি যখন সেই
বস্তু স্পর্শ করে, তখন সে ওই শক্তির ছাপগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম
হয়।
এই ধারণাটি অতিপ্রাকৃতিক অনুসন্ধান থেকে শুরু করে জনপ্রিয় গল্প বলার ধারায়ও
বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভৌতিক ঘটনা তদন্তে অনেক সময় সাইকিকরা সেই ঘটনার সাথে
জড়িত কোনো বস্তুতে সাইকোমেট্রি প্রয়োগ করে তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। আবার
সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে এটি এমন এক নাটকীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা
চরিত্রদের দ্রুত কোনো গুরুত্বপূর্ণ অতীত ঘটনার সূত্রে পৌঁছে দেয়।
সাইকোমেট্রি সঠিক কি না তা যাচাই করার জন্য কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা চালানো
হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা অজানা কোনো বস্তুর সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে
সঠিক তথ্য (যেমন মালিকের তথ্য বা সেই বস্তু সম্পর্কিত অতীত অভিজ্ঞতা) দিতে
পেরেছেন। তবে সংশয়বাদীদের মতে, এ ধরনের ফলাফল আসলে কাকতালীয় মিল, অনুমান কিংবা
অংশগ্রহনকারীদের নিজেদের অজান্তেই বস্তুগুলো নিয়ে সূক্ষ্ম সংকেত ধরে ফেলার ফলাফল
হতে পারে।
অ্যানিমেল টেলিপ্যাথিঃ প্রাণীদের সঙ্গে মনের যোগাযোগ
কিছু সাইকিক দাবী করেন যে তারা মানসিকভাবে প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন,
তাদের আবেগ অনুভব করতে পারেন কিংবা তাদেরকে শান্ত করার মতো চিন্তা প্রাণীদের মনে
পৌঁছে দিতে পারেন। এ অভিজ্ঞতাকে প্রায়ই শব্দহীন এক ধরনের যোগাযোগ হিসেবে দেখা
হয়, যেখানে মানুষ ও পশুপাখিদের মধ্যে ছবি, অনুভূতি ও ধারণার আদান-প্রদান ঘটে।
সাইকিকদের মতে, এর মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণী একে অপরের সঙ্গে আরও গভীর ও মানসিক
স্তরে যোগাযোগ করতে পারে।
অনেক পোষা প্রাণীর মালিক দাবি করেন যে তারা তাদের প্রাণীর অনুভূতি বুঝতে পারেন।
তারা বলেন, যখন তাদের পোষা প্রাণীরা উদ্বিগ্ন, অসুস্থ বা যত্ন প্রয়োজন মনে করে,
তখন তারা তা কোনো স্পষ্ট সংকেত ছাড়াই অনুভব করতে পারেন। এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলোই
প্রমাণ দেয় যে, মানুষ-প্রাণীর সম্পর্ক সাধারণ পর্যবেক্ষণের বাইরে আরও গভীর হতে
পারে।
উন্নত বিশ্বে কখনো কখনো নিজদের প্রাণীদের সাথে যোগাযোগকারী দাবী করা লোকেরা
পশুচিকিৎসক বা উদ্ধার সংস্থার সঙ্গে কাজ করেন। তারা দাবি করেন যে অ্যানিম্যাল
টেলিপ্যাথি ক্ষমতার সাহায্যে তারা হারিয়ে যাওয়া প্রাণীর অবস্থান নির্ধারণ করা,
স্বাস্থ্যের সমস্যা বা আচরণগত জটিলতা শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারেন। এইভাবে
প্রাণী টেলিপ্যাথিকে কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, বরং একটি ব্যবহারিক উপকরণ
হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়।
অ্যানিমেল টেলিপ্যাথি ক্ষমতায় বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রাণীদের সাথে সফল মানসিক
যোগাযোগের বহু গল্প প্রচলিত আছে। কেউ বলেন যে তারা প্রাণীদের দেখা বা অনুভূত
বিষয়ের মানসিক “ছবি” পেয়েছেন। আবার কেউ দাবী করেন যে তাদের শান্ত করার
চিন্তাভাবনা ভীত বা আক্রমণাত্মক প্রাণীকে শান্ত করতে সাহায্য করেছে।
তবে সংশয়বাদীরা এসব ঘটনা ব্যাখ্যা করেন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, সহমর্মিতা বা
মালিকের নিজের অনুভূতিকে প্রাণীর উপর আরোপ করার মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিকভাবে,
প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগের কোনো প্রমাণিত প্রক্রিয়া নেই।
তাই মূলধারার গবেষকরা সাধারণত এ ধরনের ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই বিবেচনা করেন।
সাইকিক হিলিংঃ মানসিক শক্তি ব্যবহার করে রোগীকে সারিয়ে তোলা
সাইকিক হিলিং (Psychic Healing), যাকে আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও বলা হয়ে থাকে, এমন
একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যের দেহে রোগ নিরাময় করার জন্য মানসিক
শক্তি প্রেরণ করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শরীর ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য, সুর ও
সুস্থতা ফিরিয়ে আনা। এই রীতির অনুশীলনকারীরা বিশ্বাস করেন যে মানসিক শক্তির সঠিক
প্রবাহ সরাসরি মানুষের সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলে।
রেইকি,
প্রানিক হিলিং
ও
থেরাপিউটিক টাচ
এই প্রক্রিয়ার পরিচিত কিছু কৌশল। প্রতিটির নিজস্ব ধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতি থাকলেও
সবার উদ্দেশ্য একইঃ শক্তি প্রবাহের মাধ্যমে বাধা দূর করে শরীর ও মনের সামঞ্জস্য
ফিরিয়ে আনা। এসব বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির মূল ধারনা হলো যে প্রাকৃতিক শক্তি অবাধে
প্রবাহিত হতে পারলেই তা রোগ নিরাময় প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে।
তবে আধুনিক মূলধারার চিকিৎসাশাস্ত্র সাইকিক হিলিংকে এখনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা
হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। সংশয়বাদীদের মতে, এসব চিকিৎসার ফলে রোগীরা আপাতদৃষ্টিতে
সাময়িক সময়ের জন্য যেসব সুফল পেয়ে থাকে তা মূলত প্লাসিবো (প্লাসিবো হলো এমন ভুয়া ওষুধ বা চিকিৎসা, যার কোনো প্রকৃত কার্যকর উপাদান নেই,
কিন্তু বিশ্বাসের কারণে রোগীদের মধ্যে আসল চিকিৎসার মতোই প্রভাব তৈরি করতে
পারে) নামের এক প্রকারের মানসিক প্রভাবের ফল। আর পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাবই
এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তবুও কিছু গবেষণা দেখিয়েছে যে সাইকিক হিলিং শারীরিক শিথিলতা, মানসিক চাপ হ্রাস
এবং সুস্থতার অনুভূতি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। ইতিবাচক প্রত্যাশা ও
ব্যক্তিগত যত্ন প্রায়ই দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানসিক ভারসাম্যকে
শক্তিশালী করে। তাই সাইকিক হিলিং অনেক রোগীদের জন্য সান্ত্বনা, আশা এবং
আধ্যাত্মিক সংযোগের অনুভূতি এনে দেয়।
শেষ কথা
অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাগুলো আমাদের বিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্যে, আধ্যাত্মিকতা ও
বিজ্ঞানের সংযোগস্থলে এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক উদ্ভাবনের মিলনের জায়গায়
অবস্থান করে। টেলিপ্যাথি থেকে শুরু করে সাইকিক হিলিং পর্যন্ত দাবী করা প্রতিটি
ক্ষমতা মানুষের আশা, ভয় এবং মনের অসীম সম্ভাবনার প্রতি আমাদের কৌতূহলকে ফুটিয়ে
তোলে।
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সীমিত থাকা সত্ত্বেও অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাগুলোর প্রতি
দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা দেখায় যে এর মূল আকর্ষণ হল এই ক্ষমতাগুলোর রহস্যময়
চরিত্র, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীতে এখনও অনেক রহস্যময় এবং অজানা জিনিস
রয়ে গেছে। বাস্তব বা কল্পিত যাই হোক না কেন, অতিপ্রাকৃতিক মানসিক ক্ষমতাগুলো
আমাদের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করে এবং বাস্তবতার প্রতি
আমাদের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।
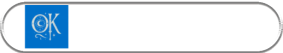








অতিপ্রাকৃতিক ব্লগের নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url