বিভিন্ন সভ্যতায় মহাপ্লাবনের বর্ননা
ইতিহাসের পাতাজুড়ে পৃথিবীর নানা সংস্কৃতিতে এমন প্রলয়ঙ্কর বন্যার কাহিনি পাওয়া
যায়, যেই প্লাবন একাধারে পুরনো সভ্যতাগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে, পৃথিবিকে শুদ্ধ
করেছে, এবং কখনো কখনো মানুষকে নতুন করে বিশ্বকে গড়ার প্রেরণা দিয়েছে।
মেসোপটেমিয়া, ভারত, চীন, আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওশেনিয়াসহ বহু অঞ্চলের পুরাণ ও
লোককথায় এই বিপুল বন্যার কিংবদন্তি গভীর ছাপ রেখে গেছে।
বর্ণনার দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও এসব গল্পে সাধারণত ঈশ্বরের ক্রোধ, এক বা একাধিক
নির্বাচিত বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি এবং জীবনের পুনর্জন্ম বা পুনর্নির্মাণের মতো
উপাদান দেখা যায়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার মহাপ্লাবন নিয়ে তাদের
নিজস্ব কাহিনীগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে, এদের মধ্যকার থিমগত মিল বিশ্লেষণ করা
হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে এমন গল্প এত বিস্তৃত কেন; সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা
করা হয়েছে।
সূচীপত্রঃ বিভিন্ন সভ্যতায় মহাপ্লাবনের বর্ননা
- মেসোপটেমিয়ান মহাপ্লাবনের কাহিনী
- হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
- প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক কাহিনিতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
- চাইনিজ পৌরাণিক কাহিনীতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
- উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের লোককথায় মহাপ্লাবনের গল্প
- আফ্রিকান আদিবাসীদের লোককথায় মহাপ্লাবনের গল্প
- পলিনেশিয়ান পৌরাণিক কাহিনীতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
- মহাপ্লাবনের গল্প নিয়ে বিভিন্ন সভ্যতার কাহিনীতে যেসব উপাদানের মিল পাওয়া যায়
- মহাপ্লাবনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলো
- শেষ কথা
মেসোপটেমিয়ান মহাপ্লাবনের কাহিনী
প্রাচীন মেসোপটেমিয়া (বর্তমানের ইরাক) থেকে উদ্ভূত একটি মহাপ্লাবনের গল্পকে
বিশ্বের প্রাচীনতম ও প্রভাবশালী কাহিনিগুলোর একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই
কাহিনীটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ সালে রচিত হওয়া
গিলগামেশের মহাকাব্য বইটিতে পাওয়া যায়। এতে গিলগামেশ নামে এক বীর
রাজা তার প্রিয় বন্ধু এনকিদুর (Enkidu) মৃত্যুর পর অমরত্বের রহস্য জানতে বের হন,
আর সেই অভিযানের পথে তিনি এক মহাপ্রলয়ঙ্কারি বন্যার কাহিনি জানতে পারেন।
গিলগামেশ তার অমরত্বের সন্ধানে যাত্রা করতে গিয়ে উতনাপিশতিম (Utnapishtim) নামের এক ব্যক্তির খোঁজ পান, যিনি দেবতাদের ইচ্ছায় চিরজীবনের অধিকারী
হয়েছিলেন। উতনাপিশতিম জানান যে তিনি দেবতাদের পক্ষ থেকে মানবজাতির উপর একটি ধ্বংসাত্মক শাস্তি
হিসেবে পাঠানো এক প্রলয়ঙ্কারি বন্যা থেকে তিনি বেঁচে যান।
উতনাপিশতিমের বর্ণনায় জানা যায়, মানুষ দিনে দিনে ক্রমেই অশান্ত ও অবাধ্য হয়ে উঠছিল যার
ফলে তারা দেবতাদের রোষের শিকার হন। এর ফলেই তারা মানবজাতিকে এক ভয়ংকর বন্যার
মাধ্যমে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঈশ্বরীয় বিচার একধরনের নৈতিক অবক্ষয়ের
প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় যেখানে মানুষের আচরণই তার নিজ ধ্বংসের কারণ
হয়ে দাঁড়ায়।
তবে দেবতা এয়া (Ea) উতনাপিশতিমের প্রতি করুণা দেখান এবং গোপনে তাকে আসন্ন বিপদের কথা জানান। তিনি
উতনাপিশতিমকে একটি বিশাল নৌকা নির্মাণ করতে নির্দেশ দেন যেখানে তার পরিবার এবং সব
ধরনের জীবজন্তুর প্রতিটি প্রজাতির একজোড়া করে রাখা যাবে। এয়ার এই সতর্কতা ও
নির্দেশনার ফলে ভয়াবহ ধ্বংসের মধ্যেও পৃথিবীতে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
সম্ভব হয়।
বন্যা থেমে গেলে উতনাপিশতিমের নৌকা
মাউন্ট নিসির
চূড়ায় এসে থামে। এরপর তিনি বন্যার পানি কমেছে কি না তা জানার জন্য একে একে
একটি কবুতর, একটি আবাবিল পাখি ও একটি কাক ছেড়ে দেন। এদের মধ্যে কেউ ফিরে আসে, কেউ
আসে না, আর এই প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে তিনি কোথায় জমি শুকিয়েছে এবং কোথায়
আশ্রয় নেওয়া সম্ভব তা বুঝতে পারেন।
উতনাপিশতিমের কাহিনিতে এমন অনেক প্রতীকী ও আদর্শ উপাদান রয়েছে, যা পরবর্তী
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাহিনিগুলোর মধ্যে বারবার ফিরে এসেছে। যেমন ঈশ্বরের রোষ,
একজন নির্বাচিত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, একটি নৌকার নির্মাণ, জীবনের সংরক্ষণ এবং
স্থলভূমির খোঁজে পাখির ব্যবহার। এই উপাদানগুলো সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য
মহাপ্লাবন সম্পর্কিত মিথগুলোতে নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু মূল
থিমগুলি একই থেকেছে।
হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
হিন্দু পুরাণে প্রলয়ের কাহিনি প্রথম পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণ-এ, যাকে পরে
বিভিন্ন পুরাণেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছেন মনু, যিনি
হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র অনুসারে মানবজাতির প্রথম পুরুষ ও প্রজাপিতা হিসেবেও পরিচিত।
তাঁর গল্প হিন্দুধর্মে শুধু একটি প্রলয় থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা নয়, বরং সৃষ্টির
পুনর্জাগরণ ও মানবজাতির ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত
হয়ে আসছে।
পুরান অনুসারে একদিন মনু যখন নদীর ধারে পূজা অর্চনা করছিলেন, তখন তিনি নিজের
জলপাত্রে একটি ছোট মাছ দেখতে পান। মাছটি বড় বড় জলজ প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা
পাওয়ার জন্য তার কাছে আশ্রয় চায়। মনু সহানুভূতিশীল হয়ে মাছটিকে একটি পাত্রে
রাখেন; কিন্তু মাছটি ক্রমশ বড় হতে থাকলে তিনি সেটিকে বড় পাত্রে, তারপর ধীরে
ধীরে একটি পুকুর, নদী এবং শেষে সমুদ্রে স্থানান্তর করেন।
অবশেষে মাছটি দেবতা বিষ্ণুর এক অবতার হিসেবে নিজের সত্য পরিচয় প্রকাশ করে। বিষ্ণু
মনুকে সতর্ক করেন যে এক ভয়াবহ প্রলয় আসতে চলেছে যা পৃথিবীর সব জীবকুলকে ধ্বংস
করে দেবে। তিনি মনুকে একটি মজবুত নৌকা তৈরি করতে নির্দেশ দেন, যাতে এই ধ্বংসের
মধ্যেও সে জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা পেতে পারে।
দেবতার নির্দেশ অনুসারে মনু একটি বিশাল নৌকা নির্মাণ করেন। তিনি সঙ্গে নেন সাতজন
ঋষি, সব ধরনের উদ্ভিদের বীজ, এবং প্রতিটি প্রাণীর একটি করে জোড়া। এই প্রস্তুতির
লক্ষ্য ছিল প্রলয়ের পরে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সংরক্ষণ
করা, যাতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
প্রলয়ের জল যখন পৃথিবীকে গ্রাস করতে শুরু করে, তখন সেই মাছটি বিশাল রূপ ধারণ করে
মনুর কাছে ফিরে আসে। সে তার শিঙে মনুর নৌকাটি বেঁধে নেয় এবং ঝড়ো জলের মধ্যে
নিরাপদে টেনে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে ভেসে চলার পর নৌকাটি এক পর্বতের চূড়ায়
এসে থামে, যাকে অনেক সময় হিমালয় পর্বত বলে চিহ্নিত করা হয়।
জল সরে যাওয়ার পর মনু দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং বেঁচে থাকার
জন্য তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানান। এই যজ্ঞ মানবজাতির এক নতুন যুগের সূচনা চিহ্নিত
করে। মনু ও তার সঙ্গে থাকা জীবদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আবার জীবন ছড়িয়ে
পড়ে।
হিন্দু পুরাণের এই প্রলয় কাহিনীর সাথে মহাপ্লাবন নিয়ে চলে আসা অন্যান্য গল্পের
সঙ্গে অনেক মিল আছে (যেমন ঈশ্বরীয় সতর্কবার্তা, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি,
জীবনের সংরক্ষণ এবং এক নতুন সূচনা)। তবে এটি হিন্দু দর্শনের এক বিশেষ
দৃষ্টিভঙ্গিকেও তুলে ধরে, যেখানে ধর্মপালন, বিশ্বাস এবং ব্রহ্মাণ্ডীয় চক্রের
ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনুর আনুগত্য ও বিষ্ণুর দিকনির্দেশনার মধ্য
দিয়ে এই কাহিনী সংকটের মুহূর্তে ধর্ম, ঐশ্বরিক নিয়ম এবং বিশ্বাসের শক্তিকে
বিশেষভাবে আলোকিত করে।
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক কাহিনিতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
রোমান কবি ওভিডের বিখ্যাত কাব্য মেটামরফোসিস-এ গ্রিক পুরাণে মহাপ্লাবনের
কাহিনি বিশেষভাবে বর্ননা করা হয়েছে। এই কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছেন দেবরাজ জিউস,
যিনি মানুষের অবাধ্যতা ও নৈতিক অবক্ষয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। মানবজাতির এই পতনে
বিরক্ত হয়ে তিনি এক প্রলয়ঙ্কর বন্যার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে সব মানুষকে ধ্বংস
করার সিদ্ধান্ত নেন।
এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা জানতে পেরে প্রমিথিউস, যিনি গ্রীক মিথোলজি অনুসারে মানব
জাতির স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত, তাঁর ধার্মিক পুত্র ডিউকেলিয়নকে সতর্ক করেন।
ডিউকেলিয়ন ও তাঁর স্ত্রী পির্রাহ, যারা উভয়েই ধার্মিক ও সদাচারী ছিলেন, একটি
বড় কাঠের বাক্স বা নৌকা তৈরির উপদেশ পান। তারা সেই পরামর্শ মেনে নৌকা তৈরি করেন
এবং আসন্ন প্রলয়ের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।
প্রলয় শুরু হলে চারপাশের সব মানুষ পানিতে তলিয়ে যায়; কেবল ডিউকেলিয়ন ও পির্রাহ
নৌকার আশ্রয়ে বেঁচে থাকেন। তারা কয়েকদিন ধরে উত্তাল সাগরে নৌকায় ভেসে থাকেন
এবং পৃথিবীর স্থলভাগের সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডুবে যাওয়ার দৃশ্যের সাক্ষী হন।
অবশেষে পানি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে এবং তাদের নৌকা পারনাসাস পর্বতের চূড়ায়
এসে থামে।
পৃথিবী তখন সম্পূর্ণ সুনসান, জনশূন্য অবস্থায় ছিল। ডিউকেলিয়ন ও পির্রাহ তা দেখে
গভীরভাবে বিষণ্ণ ও একাকী বোধ করেন। তারা মানবজাতিকে কীভাবে আবার সৃষ্টি করা যায়,
সেই বিষয়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন। তখন দেবী থেমিস তাদেরকে রহস্যময় একটি
উপদেশ দেনঃ "তোমাদের মায়ের হাড় পিছন দিকে ছুঁড়ে ফেলো।"
প্রথমে তারা দেবীর এই রহস্যময় নির্দেশে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তবে পরে তারা
বুঝতে পারেন, এখানে 'মা' বলতে পৃথিবীকে, আর 'হাড়' বলতে পাথর বা মাটিকে বোঝানো
হয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তারা পেছন দিকে পাথর ছুঁড়ে দিতে থাকেন। অবাক করা
ব্যাপার হলো, ডিউকেলিয়নের ছোড়া পাথর থেকে পুরুষ আর পির্রাহর ছোড়া পাথর থেকে
নারী জন্ম নিতে থাকে। এভাবেই আবার নতুন করে মানবজাতির সূচনা হয়।
এই প্রতীকধর্মী নবজন্মের কাহিনিটি গ্রিক মহাপ্লাবনের গল্পকে অন্যান্য সংস্কৃতির
প্রলয়ের কাহিনী থেকে আলাদা করে তোলে। এখানে মানবজাতির পুনর্জন্ম শারীরিক প্রজননের
মাধ্যমে নয়, বরং প্রতীকী রূপান্তরের মাধ্যমে ঘটে। এই কাহিনী দেখায়,ঈশ্বরের
নির্দেশনা, প্রতীকী কর্ম এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই নতুন জীবন শুরু করা
সম্ভব।
চাইনিজ পৌরাণিক কাহিনীতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
চীনা পুরাণে একাধিক প্রলয়ের কাহিনী থাকলেও, এর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী
গল্পগুলোর একটি হলো 'ইউ দ্য গ্রেট' (Yu the Great)-এর কাহিনী। এই বীর পুরুষের
গল্প পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রন্থ শান হাই জিং (পর্বত ও সাগরের গ্রন্থ) এবং
ঐতিহাসিক দলিল শি জি (Records of the Grand Historian)-তে। অন্যান্য
সংস্কৃতির মহাপ্লাবনের কাহিনিতে যেখানে মানুষ নৌকায় চড়ে বেঁচে থাকে, সেখানে চীনা
সংস্করণে ইউ-এর ভূমিকাই আলাদা। ইউ এর গল্পে দেবতারা তাঁকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ
নিয়ন্ত্রণ করে মানবজাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেন।
এই কাহিনির শুরু এক ভয়াবহ বন্যা দিয়ে, যা প্রাচীন চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে
প্লাবিত করে তোলে। বন্যার তোড়ে ক্ষেতখামার, বসতভিটা, এমনকি পুরো জনপদ ধ্বংস হয়ে
যায়। তখন দেবতারা একজন বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে
ইউ-কে বেছে নেন যিনি এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং আবারও দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে
আনবেন।
ইউ কোনো অলৌকিক কৌশল বা নৌকার সাহায্যে বন্যা মোকাবিলা করেননি। বরং তিনি নিজের
শ্রম, জ্ঞান আর ধৈর্যের উপর নির্ভর করে কাজ শুরু করেন। বছরের পর বছর তিনি চীনের
বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে ভূমির প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেন এবং সাধারণ মানুষের
সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। তিনি খাল খনন, বাঁধ নির্মান এবং পানি
নিষ্কাশনের একটি জটিল ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, যা বন্যার পানিকে সঠিকভাবে নদী ও সাগরে
প্রবাহিত করতে সাহায্য করে।
ইউ এর বাবা গুন (Gun) বন্যা থামাতে বড় বড় বাঁধ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তাতে কাজ
হয়নি। ইউ বুঝতে পারেন, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই না করে, বরং তার সঙ্গে মিলে কাজ
করলেই সাফল্য আসে। তাই তিনি পানি প্রবাহের স্বাভাবিক পথকে বাধা না দিয়ে, বরং সেই
পথগুলো পরিষ্কার ও নিয়ন্ত্রিত করে দেন। তাঁর এই বাস্তবমুখী চিন্তাভাবনা সফল হয়
এবং ধীরে ধীরে বন্যার পানি নামতে শুরু করে।
ইউ শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণ করেই থেমে যাননি, বরং তিনি একই সাথে চীনে কৃষিনির্ভর
সমাজ গড়ে তোলার ভিত্তিও তৈরি করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত হয় এবং
একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূচনা ঘটে। এই পথ ধরেই চীনের প্রথম
কিংবদন্তিপূর্ণ শিয়া (Xia) রাজবংশের সূচনা ঘটে। এই জন্য চীনের ইতিহাসে ইউ দ্য
গ্রেটকে একজন জ্ঞানী রাজা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক হিসেবে স্মরন করা
হয়।
চীনা মহাপ্লাবনের কাহিনী অন্যান্য কাহিনির চেয়ে আলাদা, কারণ এখানে ঈশ্বরের ক্রোধ
বা অলৌকিক মুক্তির চেয়ে মানুষের মেধা, পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্পের ওপর জোর দেওয়া
হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে এখানে ঈশ্বর বা অতিপাকৃতিক শক্তির প্রতিশোধ নয়, বরং
মেধা ও শ্রম দিয়ে তা মোকাবিলা করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখা হয়েছে। ইউ দ্য গ্রেট
এর এই সাফল্য আমাদের শেখায় যে সহযোগিতা, ধৈর্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে
চলাই এই পৃথিবীতে টিকে থাকার মূল চাবিকাঠি।
উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের লোককথায় মহাপ্লাবনের গল্প
উত্তর আমেরিকার অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মহাপ্লাবনের গল্প রয়েছে, যা
তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। উদাহরন স্বরূপ,
হোপি জনগণের (The Hopi) লোক কথাতে দেখা যায় যে একবার পৃথিবী এতটাই
দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে এক মহাপ্লাবনের মাধ্যমে তা ধ্বংস হয়। তবে কিছু
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ফাঁপা নলখাগড়া/পাটকাঠির ভেতরে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বাঁচেন।
এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি কেবল ব্যক্তিগত
নয়, গোটা মানবজাতির টিকে থাকার জন্যও অপরিহার্য।
আবার, ওজিবওয়ে জাতিগোষ্ঠীর (The Ojibwe) বিশ্বাস অনুযায়ী, এক সময় পুরো পৃথিবী
মহাপ্লাবনে ডুবে গিয়েছিল, এবং কেবল কয়েকটি পশুই কোনোভাবে বেঁচে ছিল। তাদের গল্প
অনুসারে একটি বিশাল কচ্ছপের পিঠে নতুন করে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়, যা তাদের
সংস্কৃতিতে সহনশীলতা ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা
করা হয়ে থাকে। পৃথিবীকে কচ্ছপের পিঠে ধরে রাখার এই ধারণা শুধু ওজিবওয়ে নয়, বরং
ইরোকোয়িসসহ (The Iroquois) আরও অনেক উত্তর আমেরিকান আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর
বিশ্বাসেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।
উত্তর আমেরিকার ম্যান্ডান জাতিগোষ্ঠী (The Mandan) বিশ্বাস করে এক মহাপ্লাবনে
সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যায়, এবং সেই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে কেবল একজন মানুষ একটি
বিশাল ক্যানোর (এক ধরনের নৌকা) ভিতরে বেঁচে থাকতে সক্ষম হন। তাঁর বেঁচে থাকাই
পৃথিবীতে নতুন জীবনের পুনর্জাগরণের সূচনা হয়ে ওঠে। উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের
মধ্যে প্রচলিত এ ধরনের বন্যার কাহিনিগুলো প্রকৃতির প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ,
মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের পরিণতি এবং প্রাণীদের সৃষ্টিতে ঈশ্বরের পবিত্র ভূমিকার
মতো মৌলিক শিক্ষাকে আমাদের সামনে গভীরভাবে তুলে ধরে।
আফ্রিকান আদিবাসীদের লোককথায় মহাপ্লাবনের গল্প
আফ্রিকান মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করা আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মৌখিক ঐতিহ্যেও
মহাপ্লাবনের গল্প রয়েছে, যা তাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার গভীর বার্তা বহন
করে। উদাহরন স্বরূপ, নাইজেরিয়ার ইউরোবা জনগোষ্ঠীর এক প্রাচীন কাহিনিতে বলা হয়েছে
যে সমুদ্রের দেবতা ওলোকুন একসময় মানবজাতির উপর প্রচন্ড রাগ করে গোটা পৃথিবীকে
বন্যার পানিতে ভাসিয়ে দেন। তাদের মতে এই ঘটনাটি মানুষের কাছে সতর্কবার্তা হয়ে
আসে যে প্রকৃতির ক্ষমতা অপরিসীম, আর উচ্চতর শক্তিকে অসম্মান বা উসকে দেওয়ার
পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।
আরেকটি আফ্রিকান কিংবদন্তিতে এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যিনি একটি ভয়াবহ
প্লাবনের সময়ে একটি ছোট ডিঙিতে চড়ে কোন রকম ভাবে বেঁচে যান। সেই সময়ে তার
সাথে কয়েকটি প্রাণী ছিল যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার বন্ধনকে নির্দেশ করে। এমন
গল্পগুলো শুধু বেঁচে থাকার কাহিনি নয়; এটি ঈশ্বরের কৃপা, প্রজ্ঞা এবং প্রকৃতির
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের গভীর বার্তা বহন করে।
পূর্ব আফ্রিকার কিছু প্রাচীন কাহিনিতে মহাপ্লাবনকে কখনোই ঈশ্বরের রোষ বা শাস্তি
হিসেবে দেখা হয় না; বরং এটিকে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে মেনে
নেওয়া হয়। এসব গল্পে বলা হয়, প্রকৃতির শক্তি কারও পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, এটি
সবার জন্য সমান আচরণ করে থাকে। তাই মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই না করে, তার
সঙ্গে মানিয়ে চলতে শেখা উচিত।
পলিনেশিয়ান পৌরাণিক কাহিনীতে মহাপ্লাবনের বর্ননা
পলিনেশিয়ান (প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে একত্রে
পলিনেশিয়া বলা হয়; এ সমস্ত দ্বীপগুলোতে বসবাস করা আদিবাসী এবং তাদের ভাষা ও
সংস্কৃতিকে পলিনেশিয়ান বলা হয়ে থাকে) পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী মানুষ পবিত্র আইন,
যাকে স্থানীয় ভাষায় তাপু বলা হয়,ভঙ্গ করলে দেবতারা মহাপ্লাবন ডেকে এনে
তাদেরকে শাস্তি দিতেন। এই গল্পগুলো পলিনেশিয়ান সমাজে নৈতিক শিক্ষার মতো কাজ করত;
এসব গল্প তাদেরকে সতর্ক করত যে দেবতাদের প্রতি অবাধ্যতা ও অসম্মান মানুষের জীবনের
বিপদ ডেকে আনে। এগুলো আরও বোঝায় যে দেবতারা মানুষের ভাগ্য গঠনে সক্রিয়
ভূমিকা পালন করেন।
প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপের আদিবাসীদের লোককথায় তাদের দ্বীপে দেবতা কেইনের
পাঠানো এক মহাপ্লাবনের বর্ননা রয়েছে। লোককথা অনুযায়ী দেবতা কেইনের রোষে আকাশ কালো
হয়ে আসে, সাগরের জল উথালপাথাল হয়ে উঠে, আর বিশাল ঢেউ দ্বীপের সবুজ ভূমি,
পাহাড়, বন, গ্রাম গ্রাস করে ফেলে; এর ফলে দ্বীপের অসংখ্য মানুষ ও পশুপাখি প্রান
হারায় এবং প্রাচীন বসতিগুলো চিরতরে হারিয়ে যায়। নিজেদের প্রাণ, বংশ ও
সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কেবল কয়েকজন মানুষ নৌকায় পালিয়ে বেঁচে যান।
নিউজিল্যান্ডের মাউরি আদিবাসীদের লোককথায় প্রায়ই দেখা যায় যে মানবজাতির অন্যায়,
অহংকার বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার শাস্তি হিসেবে কোনো দেবতা বা
অতিপ্রাকৃতিক সত্তা প্রলয় ঘটান। মাওরিরা বিশ্বাস করে যে পরিবেশের প্রতিটি
উপাদানের সাথে ( যেমন পানি, মাটি, আকাশ, বন) তাদের পূর্বপুরুষের আত্মারা জড়িয়ে
আছে। তাই প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা মানে পূর্বপুরুষকে অসম্মান করা, যা সবশেষে
মানুষের উপরে দেবতাদের ক্রোধ ডেকে আনে।
মহাপ্লাবনের গল্প নিয়ে বিভিন্ন সভ্যতার কাহিনীতে যেসব উপাদানের মিল পাওয়া যায়
ভিন্ন ভিন্ন সময় এবং সংস্কৃতিতে উৎপত্তি হলেও বিশ্বের নানা প্রান্তের মহাপ্লাবনের
গল্পগুলোতে বিস্ময়কর মিল লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলঃ
১। দেবতা/ঐশ্বরিক শক্তির অসন্তোষঃ বহু প্লাবনের কাহিনিতে দেখা যায়, কোনো এক দেবতা বা দেবগোষ্ঠী মানবজাতির
আচরণে গভীরভাবে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধ সাধারণত মানুষের নিজেদের মধ্যে সহিংসতা,
অতিরিক্ত অহংকার, বা দেবতার প্রতি স্পষ্ট অবমাননা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। এর
ফলস্বরূপ, সেই দেবতা বা ঐশ্বরিক শক্তি পৃথিবীকে মানব জাতির দূষণ থেকে শুদ্ধ করতে
এক মহাবিপর্যয়কর প্লাবন প্রেরণ করেন।
২। নির্বাচিত ব্যাক্তিঃ এসব কাহিনিতে প্রায়শই এক বা কয়েকজন মানুষ
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাদের বেঁচে থাকার পেছনে সাধারণত অসাধারণ পুণ্য,
গভীর প্রজ্ঞা, বা দেবতার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের কথা বলা হয়। এই নির্বাচিত
ব্যক্তিরাই বিপর্যয়ের পর মানবজাতিকে পুনর্গঠনের প্রধান ভূমিকা পালন করে।
৩। বিশেষ নৌযানঃ অনেক কাহিনিতে দেখা যায়, বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে তৈরি নৌকা, ভেলা বা
আর্ক ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কিছু লোককথায় মানুষ এমন কোনো পবিত্র পর্বতে বা
নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে যা প্লাবনের নাগালের বাইরে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই
নৌযান বা আশ্রয় কেবল শারীরিক মুক্তির প্রতীকই নয়, বরং এগুলো মানুষের আধ্যাত্মিক
পরিত্রাণেরও প্রতীক হয়ে ওঠে।
৪। জীবনের সংরক্ষনঃ মানব জীবিতদের পাশাপাশি অনেক কাহিনিতে পশুপাখি
এবং কখনও কখনও উদ্ভিদও রক্ষা করা হয়, যাতে প্লাবনের পরে জীবনধারা অব্যাহত থাকে।
এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রায়শই জোড়ায় জোড়ায় প্রাণী সংগ্রহ বা প্রয়োজনীয়
উদ্ভিদের বীজ বহন করার মতো সচেতন প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই বিবরণগুলো প্লাবনের পর
জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত ভারসাম্যের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে তোলে।
৫। নতুন সুচনাঃ মহাপ্লাবনের পানি সরে গেলে ধ্বংসস্তূপের মাঝে মানবজাতির জন্য এক নতুন
অধ্যায় শুরু হয়। যারা বেঁচে থাকে তারা আবার নতুন করে পৃথিবীকে গড়ে তোলার সুযোগ
পায়। বেঁচে থাকা লোকেরা যাতে করে তাদের জীবনকে নৈতিকভাবে সৎ ও সুষম পথে চালিত
করতে পারে সেজন্যে প্রায়শই ঈশ্বর বা দেবতারা তাদের কাছে বার্তা, নির্দেশ
বা নতুন বিধি পাঠান। এই মুহূর্তটি কেবল বেঁচে থাকার গল্প নয়, বরং আশার
পুনর্জাগরণ, ভগ্ন সভ্যতার পুনর্গঠন, এবং ভবিষ্যতে আরও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের
সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে ওঠে।
মহাপ্লাবনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলো
বিভিন্ন সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে মহাপ্লাবনের কাহিনীগুলোর বিস্ময়কর মিল ও বিশ্বের
নানা প্রান্তে এর বিস্তারের কারণ ব্যাখ্যা করতে বহু তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে।
এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ব্যাখ্যা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ
১। বাস্তব মহাপ্লাবনের ঐতিহাসিক স্মৃতিঃ বহু গবেষকের মতে, প্রাচীন প্লাবনের মিথগুলো কেবল মানুষের কল্পনার সৃষ্টি
নয়, বরং সেগুলো হয়তো বাস্তব কোনো মহাবিপর্যয়কর বন্যার স্মৃতি বহন করছে। আজ
থেকে প্রায় ১২,০০০ বছর আগে বরফযুগ শেষ হয়ে যখন বিশাল হিমবাহগুলো দ্রুত গলতে শুরু
করে, তখন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। এর ফলে উপকূলীয় অঞ্চল, নদী
উপত্যকা এবং নিম্নভূমি ব্যাপকভাবে ডুবে যেতে শুরু করে।
ব্ল্যাক সি অঞ্চলের হঠাৎ জলপ্রবাহ, মেসোপটেমিয়ার নদী উপত্যকার মৌসুমি বা
অস্বাভাবিক প্লাবন, কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলীয় এলাকার বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস;
এসব ঘটনা স্থানীয় জনগণের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রজন্মের পর
প্রজন্ম ধরে মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়ে ধীরে ধীরে পৌরাণিক রূপ নেয়, যেখানে
প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মানবজাতির উপরে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত শাস্তি বা আধ্যাত্মিক
সতর্কবার্তার আকারে উপস্থাপন করা হয়।
২। প্রতীকী ব্যাখ্যাঃ বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মহাপ্লাবনকে শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে
নয়, বরং গভীর প্রতীকী অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে বন্যার পানি ধ্বংসের শক্তি
যা পুরনো, দূষিত বা অবক্ষয়িত সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; আবার একই সঙ্গে তা
শুদ্ধির মাধ্যম, যা নতুন সূচনার জন্য ভূমি ও সমাজকে প্রস্তুত করে। এই কারণে
মহাপ্লাবনের মিথকে প্রায়শই নৈতিক শুদ্ধি, চক্রাকার পুনর্জন্ম, এবং মহাজাগতিক
ভারসাম্যের নতুন করে স্থাপন করার রূপক হিসেবে দেখা হয়।
৩। সাংস্কৃতিক বিস্তারঃ কিছু ইতিহাসবিদের মতে, মেসোপটেমিয়ার মতো প্রাচীন সভ্যতার মহাপ্লাবনের
গল্প তাদের জন্মভূমি ছাড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যপথ,
অভিবাসন, এবং সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনির মূল উপাদান বিভিন্ন অঞ্চলে
পৌঁছে যায়। একবার নতুন ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয়
বিশ্বাস অনুযায়ী গল্পগুলোতে পরিবর্তন আনা হয়; কখনও চরিত্রের নাম বদলানো, কখনও
ঘটনার স্থান স্থানান্তর, আবার কখনও মূল উদ্দেশ্যকে নতুন রূপ দেওয়া হয়।
৪। মানসিক ও প্রতীকী সার্বজনীনতাঃ কার্ল ইয়ুং (Carl Jung) ও জোসেফ ক্যাম্পবেলের (Joseph Campbell)
মতো বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মতে, মহাপ্লাবনের মিথগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে
বারবার ফিরে আসে কারণ এগুলো মানুষের চেতনার গভীরে থাকা অভিন্ন মানসিক ধরণ বা
আর্কিটাইপ-কে স্পর্শ করে। মহাপ্লাবনের মিথে দেখা যায় বিচার, বেঁচে থাকা ও
নবায়নের মতো থিম, যা মানবসমাজের প্রাচীনতম ভয় (যেমন ধ্বংসের আশঙ্কা) এবং
প্রাচীনতম আশা (যেমন পুনর্জন্ম ও নতুন শুরুর আকাঙ্ক্ষা) উভয়ের সঙ্গেই
সঙ্গতিপূর্ণ।
এই থিমগুলো কেবল সাংস্কৃতিক কাহিনি নয়, বরং মানব মনের গভীরে প্রোথিত প্রতীক, যা
আপনা আপনি ভাবে বিভিন্ন সমাজে জন্ম নেয়। এই কারণেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক
প্রান্তে, এমনকি কোনো প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছাড়াই, আমরা বিভিন্ন সভ্যতার
মহাপ্লাবনের গল্পে একই ধরনের কাঠামো ও অর্থ দেখতে পাই।
শেষ কথা
বিভিন্ন সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে চলে আসা মহাপ্লাবনের মিথ মানবজাতির টিকে থাকা,
নৈতিকতা এবং প্রকৃতির অপরিসীম শক্তি নিয়ে মানুষের অভিন্ন উদ্বেগকে প্রতিফলিত
করে। বাস্তব ঘটনা, প্রতীকী অর্থ কিংবা সাংস্কৃতিক বিনিময় যেখান থেকেই উদ্ভূত হোক
না কেন, এই মিথ যুগে যুগে বিভিন্ন সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও
সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।
মেসোপটেমিয়া থেকে আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে হিমালয় পর্যন্ত
সবখানে এই মিথগুলো এক অভিন্ন সত্য প্রকাশ করেঃ জীবন ভঙ্গুর; প্রকৃতি একইসাথে
স্নেহময়ী লালনকারী ও প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক; আর মহাবিপর্যয়ের পরও নবজাগরণ
সম্ভব। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচারিত এই কাহিনিগুলো সতর্কবার্তা হওয়ার
পাশাপাশি আশার উৎস হিসেবেও কাজ করে; এই কাহিনীগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে
বিশ্বাস, স্থিতিস্থাপকতা এবং ঈশ্বর বা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে এই
পৃথিবীতে টিকে থাকা সর্বদা সম্ভব।
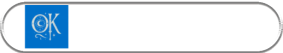













অতিপ্রাকৃতিক ব্লগের নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url